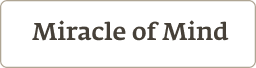মহাভারত পর্ব ১৫: পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন
মহাভারতের এই পর্বে, পাণ্ডব ভাইয়েরা তাঁদের পিতার মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরে চলে আসেন, যা দুর্যোধনের অসন্তোষের কারণ। এর সাথে আমরা শকুনির প্রতিশোধ স্পৃহার মূলে কী তা জানব - মন্ত্রঃপূত পাশা-জোড়ার সাহায্যে এই প্রতিশোধ স্পৃহা পরে চরিতার্থ হয়।
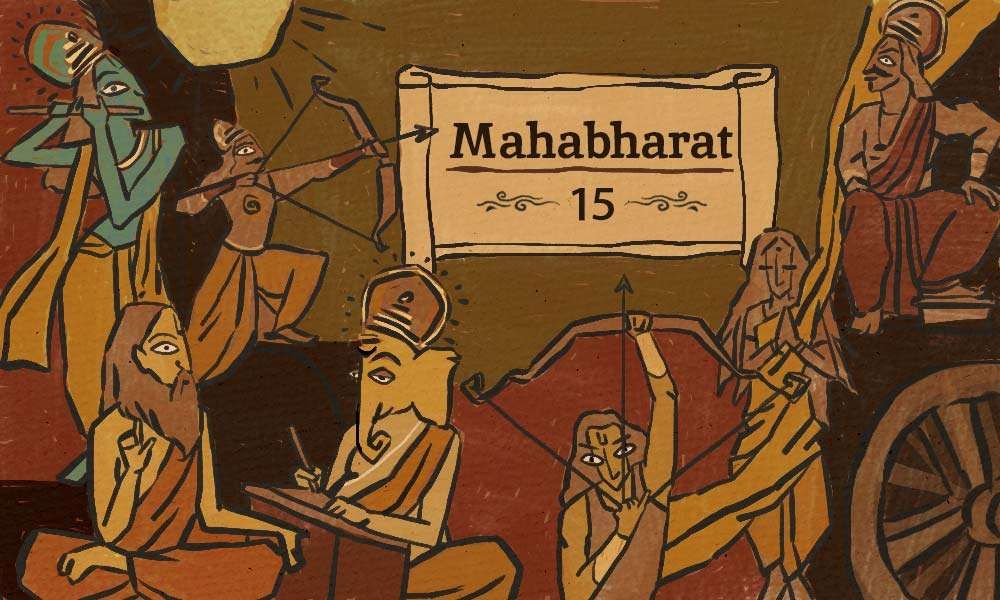
পাণ্ডবদের অরণ্যে বসবাস
সদগুরু: পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই অরণ্যে খুব ভালভাবে বেড়ে ওঠেন। যথাযথ নির্দেশনায় প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠাই কারোর জন্য সবচেয়ে ভাল শিক্ষা হতে পারে। মুনি-ঋষিরা তাঁদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন কিন্তু সর্বোপরি প্রকৃতি মাতাই তাঁদের জ্ঞান ও দৃঢ়তা প্রদান করেন। তাঁরা শক্তিশালী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বড়ো হয়ে ওঠেন।পাণ্ডু – কামনাই তাঁর নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়
তাঁদের পিতা পাণ্ডু অভিশপ্ত ছিলেন যে তিনি যদি কখনও মিলনের বাসনা নিয়ে তাঁর স্ত্রীদের সান্নিধ্যে আসেন, তিনি মারা যাবেন। সেজন্য তিনি তাঁর স্ত্রীদের অন্যভাবে সন্তান ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ষোল বছর তিনি তাঁর স্ত্রীদের থেকে দূরে ছিলেন, মুনি-ঋষিদের সংসর্গে থেকে, জ্ঞান অর্জন করে, ব্রহ্মচর্যের সাধনা অভ্যাস করে এক শক্তিশালী সত্তা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি যখন বনের মধ্যে একটা নির্জন নদীর কাছে পৌঁছোলেন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী তখন সবেমাত্র স্নান সেরে জল থেকে উঠে আসছিলেন। পাণ্ডু যখন তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখলেন, তিনি তাঁর প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি এত বছর পর আত্মহারা হয়ে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে তাঁর অনুবর্তী হয়ে পড়েন।
অভিশাপের বিষয়টা জানতেন বলে মাদ্রী প্রবলভাবে বাধা দিলেন কিন্তু নিয়তি পাণ্ডুকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল এবং মাদ্রীর বাহুডোরেই তিনি মারা গেলেন। আতঙ্কে মাদ্রী চিৎকার করে উঠলেন – আতঙ্ক কেবল স্বামী মারা যাওয়ার জন্যই নয় বরং তাঁর প্রতি পাণ্ডুর কামনাই যে তাঁকে শেষ করে দিল, আতঙ্ক সেইজন্যও। আর্তনাদ শুনে কুন্তী দৌড়ে এলেন এবং যখন দেখলেন যে কী ঘটেছে, তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। দুই সতীনের মধ্যে এত বছর ধরে যেসব আবেগ চাপা পড়ে ছিল তা সামনে উঠে এলো।
কিছুক্ষণ পর কুন্তী নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার কথা ভেবে শান্ত হলেন আর মাদ্রী নিছকই অপরাধবোধ ও হতাশার বশে, তাঁকে স্বামীর সঙ্গে যেতে হবে ভেবে চিতায় প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুক্ষণের জন্য কুন্তী ভান করলেন যেন মাদ্রীর বদলে তিনিই চিতায় উঠতে চান কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে ছিল দৃঢ়সংকল্প। রানী হিসেবে তাঁর যাকিছু করণীয় ছিল, কঠোরভাবে তিনি সেসব পালন করলেন। তারপর ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব ষোল বছরেরও কিছু বেশি সময় পর হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন।
পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন
বহুদিন কোনো যোগাযোগ না থাকা খুড়তুতো ভাইয়েরা ফিরে আসছে, এই খবর যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরে পৌঁছল, দুর্যোধনের মন ঘৃণা ও ঈর্ষার তরঙ্গে ভরে গেল। তিনি এটা ভেবেই বড়ো হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনিই হবেন রাজা। যেহেতু তাঁর পিতা দৃষ্টিতেও অন্ধ ছিলেন এবং তাঁর প্রতি স্নেহেও অন্ধ ছিলেন, একরকমভাবে তিনি ইতিমধ্যেই রাজা হয়ে উঠেছিলেন এবং নিজের ইচ্ছেমত সবকিছু করাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে এক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির - যাঁকে সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলেই মনে হচ্ছে। দুর্যোধন এটা একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর ভাইদের প্ররোচিত করতে লাগলেন, যাঁরা তাঁর তুলনায় নির্জীব ও শান্তশিষ্ট ছিলেন এবং একটা দেশ শাসন করতে গেলে যে তেজস্বীতার প্রয়োজন - তাঁদের মধ্যে সেটার অভাব ছিল। তিনি দেখলেন দুঃশাসনই সবচেয়ে উপযুক্ত সহযোগী, যে একশো জন ভাইয়ের মধ্যে দুই নম্বর।
পাণ্ডবরা এসে পৌঁছনোর আগে থেকেই এঁরা দুজনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। লোকেরা পাণ্ডুকে খুবই ভালোবাসতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যাভিষেক না হলেও সত্যিকার অর্থে তিনিই রাজা ছিলেন। তিনি দেশে সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য রাজ্য দখল করেছিলেন এবং প্রশাসনের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। ষোল বছর ধরে তিনি স্বেচ্ছা- নির্বাসনে ছিলেন এবং এখন তিনি গত হয়েছেন। তাঁর সন্তানেরা, যাঁদের তাঁরা এর আগে কোনোদিন দেখেননি, তাঁরা ফিরে আসছেন - এই ঘটননাই প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।
কৌতূহল ও অনুরাগ বশত সমস্ত রাজ্যবাসী জড়ো হয়েছিল। পাণ্ডবরা যখন তাঁদের মা কুন্তীর সাথে নগরে প্রবেশ করলেন, ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। জঙ্গলে বড় হওয়ায় ছেলেগুলি বেশ শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠেছিলেন, রাজপ্রাসাদে বেড়ে উঠলে যেরকম হতেন তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। একশোজন কৌরব ভাই, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ভীষ্ম, বিদুরসহ সকল বয়োজ্যেষ্ঠরা নগরের সিংহদ্বারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, যিনি একেবারে ছেলেবেলা থেকেই জগতকে দেখার জন্য এবং নানা সাহায্যের জন্য পাণ্ডুর ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন এবং যিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের থেকে সবসময় সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছেন - সেই ধৃতরাষ্ট্রের মনে মিশ্র আবেগের সঞ্চার হল। ভাইকে তিনি ভালবাসেন বলেই জানতেন, তবে নিজের সন্তানরা রাজা হবে না জানার পর এই মুহূর্তে তাঁর যেসমস্ত অনুভূতি হচ্ছিল, তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।
দুর্যোধন – ঘৃণার উদ্রেক
পাণ্ডবগণ ও কুন্তীকে অভ্যর্থনা জানানো হল। পাণ্ডুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হল এবং যে মুহূর্তে ছেলেরা রাজপ্রাসাদে পা দিলেন, সেই মুহূর্ত থেকে নিয়তি নিজেই উন্মোচিত হতে শুরু করল, বিশেষ করে ভীম এবং দুর্যোধনের মধ্যে - কেননা এই দুজন যুবকই ছিলেন দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। ভীম দৈত্যের মতো হয়ে বেড়ে উঠেছিলেন আর দুর্যোধনও গায়ের জোরে তাঁর সাথে ভালই পাল্লা দিতে পারতেন। ভীম জীবনে এই প্রথমবার রাজপ্রাসাদে থাকার ব্যাপারে খুবই উত্তেজিত ছিলেন। তিনি যেরকম খুশিতে ডগমগ, বোকাসোকা আনাড়ি ছিলেন - সব জায়গায় গিয়ে লোকজনদের সাথে হাসি- ঠাট্টা করা ও তাদের নিয়ে মজা করতে লেগে যেতেন আর সুযোগ পেলেই দুর্যোধন সহ সকল কৌরব ভাইদের তুলোধনা করতেন।
তাঁদের প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব ঘটেছিল যখন তাঁরা মল্লযুদ্ধের মঞ্চে প্রবেশ করেন। দুর্যোধনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেউ কোনোদিন তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। একশোজন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী আর তাঁর বয়সী আর কেউই কুস্তির মঞ্চে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। তিনি যখন দেখলেন যে ভীম একের পর এক প্রতিযোগিতা জিতে যাচ্ছেন আর সকলের প্রিয় হয়ে উঠছেন, দুর্যোধন ভাবলেন রাজপ্রাসাদে সারা পরিবারের সামনে একটা কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্য ভীমকে আমন্ত্রণ জানানোই হবে তাঁকে শায়েস্তা করার সবচেয়ে ভালো উপায়। বাকিদের ক্ষেত্রে এটা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হলেও তাঁদের দু’জনের জন্য এ হবে এক জীবন-মরণের লড়াই, কিন্তু কোনো লড়াই ছাড়াই ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁকে আছড়ে ফেলে দিলেন। দুর্যোধন একেবারেই ভেঙে পড়লেন। পরাজয়ের লজ্জা তাঁর রাগ ও ঘৃণাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল যে আবেগগুলোকে তিনি আর না পারলেন দমিয়ে রাখতে, না পারলেন গোপন করতে।
দুর্যোধন ভীমকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর মামা শকুনি একজন উপদেষ্টা হিসেবে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। ভারতবর্ষে শকুনি নামটা শঠতার সমার্থক। শকুনি ছিলেন গান্ধারীর ভাই। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর ভীষ্ম বুঝতে পারেন যে গান্ধারী কার্যত একজন বিধবা আর লোকে কানাঘুষো শুরু করে দেয়। তাঁর প্রথম স্বামী বিয়ের তিন মাসের মধ্যে মারা যাবেন – এই অভিশাপ খণ্ডানোর জন্য তিনি একটি পাঁঠাকে বিয়ে করেন এবং তারপর সেটাকে বলি দেওয়া হয়। ভীষ্ম এত রেগে গিয়েছিলেন – কুরু সাম্রাজ্যের সাথে কিনা এভাবে প্রতারণা করা হয়েছে যে তিনি গান্ধারীর পিতা ও তাঁর সব ভাইদের গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। এটা আতিথেয়তার বাড়াবাড়ি আর কি – হোটেল ক্যালিফোর্নিয়ায় যেমনটা হয় – অতিথিরা কখনও আর ফেরত যেতে পারবেন না। এবং সেযুগের ধর্ম এটাই ছিল যে, যেই বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হয়েছে কনের পরিবার যখন প্রথমবার সে বাড়িতে আসছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদেরকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে, তাঁরা চলে যেতে পারবেন না।
শকুনি – প্রতিশোধের জন্যই তার বেঁচে থাকা
সময়ের সাথে সাথে তাঁদের খাবারের পরিমাণ ক্রমশ কমতে কমতে এমন জায়গায় পৌঁছল যে তাঁরা সকলে শীর্ণকায় হয়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। এ যেন আজকালকার বিলাসবহুল হোটেলগুলোর মতো, আপনার সামনে টেবিলে অনেক থালা-বাসন সাজানো থাকে কিন্তু ঢাকনা খুললে পরে আপনি দেখবেন থালায় কেবল অল্প একটুখানি খাবার রাখা আছে। সেখান থেকে তাঁরা এই ধরণের আতিথেয়তাই পাচ্ছিলেন। কিছুদিন পর বাবা ও সব ভাইয়েরা কঙ্কালসার হয়ে পড়লেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে তাঁদের কুটুমরা তাঁদেরকে অনাহারে মারতে চাইছেন। কিন্তু কার্যত তাঁদের আতিথেয়তা তখনও জারি ছিল তাই তাঁরা চলে যেতেও পারছিলেন না – সেটাই ছিল তাঁদের ধর্ম।
তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করলেন যে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই আমৃত্যু না খেয়ে থাকবেন। তাঁরা তাঁদের সব খাবারটুকুই শকুনিকে দিয়ে দিতেন, যে ছিল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান - যাতে সে বেঁচে থেকে যাঁরা তাঁদের তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিলো তাঁদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। কথিত আছে যে শকুনির ভাইয়েরা যখন এক এক করে মারা যেতে লাগলেন, তাঁর বাবা তাঁকে মৃত ভাইদের অঙ্গগুলো খেয়ে নেওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন যাতে সে শক্তিশালী হয়ে উঠে তাঁদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। শকুনির বাবা যখন মারা গেলেন তাঁর কর্ম তাদের নিজেদের ভিটেতেই করতে হত। সেসময় তাকে যেতে দেওয়া হলো।
তো শকুনি সেখানে বসে তাঁর ভায়েদের শরীর চিরে তাঁদের যকৃৎ, বৃক্ক ও হৃদপিণ্ড খেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর বাবা পাশে পড়ে থাকা হাঁটার লাঠি দিয়ে শকুনির গোড়ালিতে এমন সজোরে আঘাত করলেন যে তাঁর গোড়ালি চিড় খেয়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?" তাঁর বাবা বললেন, "আমি তোমার গোড়ালি ভেঙে দিয়েছি যাতে তুমি সবসময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলো আর কেন তোমায় তোমার ভাইদের অঙ্গ খাওয়ানো হয়েছিল তা কক্ষনো না ভোলো। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপে এটা তোমায় মনে করাতে থাকবে যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তোমার বেঁচে থাকা।" বাবার মৃত্যুর পর কুরুবংশকে ধ্বংস করাই শকুনির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। তিনি তাঁদের উপদেষ্টা হয়ে ফিরে এলেন এবং দুর্যোধনের প্রশংসা ও বন্ধুত্বলাভ করলেন - সে ভাবত শকুনি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান।
মারা যাওয়ার আগে শকুনির বাবা তাঁকে বলে গিয়েছিলেন যে,"আমি মারা যাওয়ার পর, আমার আঙুলগুলো কেটে সেগুলো দিয়ে পাশা বানিও। আমার অতিলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমি এটা নিশ্চিত করব যে এই পাশার দান সবসময় তুমি যেমন চাইবে তেমনই যেন পড়ে। পাশাখেলায় কেউ কক্ষনো তোমায় হারাতে পারবে না – এটা একদিন তোমার খুব কাজে আসবে।" তো শকুনি তাঁর পিতার আঙুলগুলো কেটে সেগুলো দিয়ে পাশা তৈরি করলেন। যোদ্ধার মত শারীরিক গঠন তাঁর ছিল না কিন্তু এই পাশা তার সঙ্গে থাকায় তিনি মনে করতেন যে তিনি সারা পৃথিবী জয় করতে পারতেন।
শকুনি ও দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র
শকুনি দুর্যোধনের অনুগ্রহ লাভ করলেন, সে ছিল ঘৃণা ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ আর শকুনি ক্রমাগতই সেটাকে পুষ্ট করে যেতে থাকলেন। দুর্যোধন নিজে অতটা কুটিল ছিলেন না, তবে সহজেই মাথা গরম করে ফেলতেন। তিনি প্রায়শই মনের কথা মুখ ফুটে বলে ফেলতেন, বিশেষ করে তাঁর পিতার কাছে। শকুনি যখন এটা লক্ষ্য করলেন, তিনি তাকে বললেন, "দুর্যোধন, ঈশ্বর মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য নয়, বরং তার মনে কী আছে তা লুকোনোর জন্য।" শকুনির মানসিকতা ছিল এইরকম। শকুনি অনবরত দুর্যোধনের মনের বিষটাকে পোষণ করে যেতে থাকলেন আর এটা নিশ্চিত করলেন যে সেই বিষ যেন তাঁর দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তিনি দুর্যোধনকে বললেন, "তোমার যদি কোনো শত্রু থাকে, তাকে চিমটি কেটে, গালমন্দ করে, তার গায়ে থুতু দিয়ে কোনো লাভ হবে না – এটা কেবল তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। একজন বোকাই কেবল এরকম কাজ করে। যে মুহূর্তে তুমি কাউকে তোমার শত্রু বলে চিনতে পারবে - তাকে হত্যা কর।" তো দুর্যোধন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি প্রাসাদের মধ্যে কীভাবে আমার খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করব?" শকুনি নানারকম ষড়যন্ত্রের প্রস্তাব দিতে লাগলেন।
চলবে...
Editor's Note: A version of this article was originally published in Isha Forest Flower, February 2016.